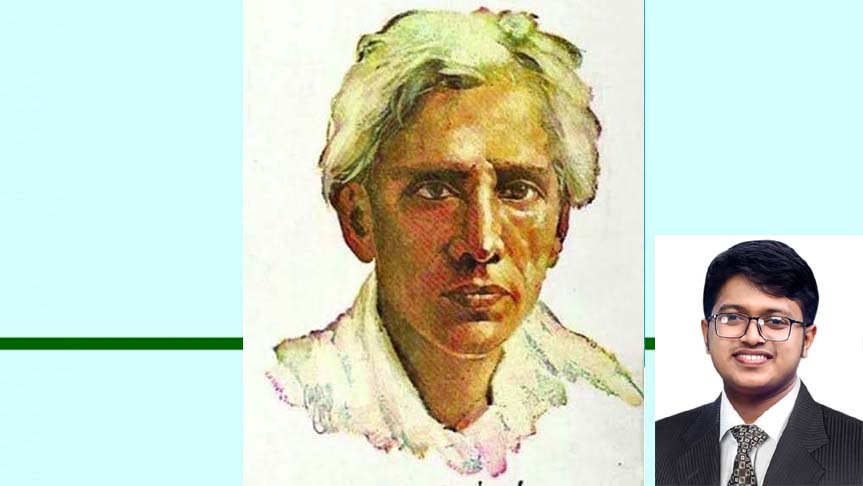-ইমরান ইমন
বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কালজয়ী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করা এই কথাশিল্পীর এবার ১৪৬তম জন্মবার্ষিকী। শরৎচন্দ্রের বাবা ছিলেন মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মা ভুবনমোহনী দেবী। বাবা ছিলেন প্রচুর বইপড়–য়া, জ্ঞানী ও সাহিত্যানুরাগী। বাবার কাছ থেকেই শরৎচন্দ্র প্রথম লেখালেখির অনুপ্রেরণা লাভ করেন।
ছোটবেলা থেকেই শরৎচন্দ্রের বইপড়া আর সবকিছু জানার নেশা ছিল। সহপাঠী এবং প্রতিবেশীরা সবসময় তার দুরন্তপনার ভয়ে থাকতো। বাড়ির লোকেরাও তার উপর বিরক্ত হয়ে ওঠেন। বনে জঙ্গলে ঘুরে নানা রকম ফড়িং ধরে একটি কাঠের বাক্সে পুরে রাখতেন। গাছে চড়া, গাছে বসেই ঘুমানো, গভীর রাতে শ্মশানঘাটে যাওয়া বা পোড়োবাড়িতে যেতে তার মোটেই ভয় করতো না। ঠাকুরদাদার আফিমের কৌটা লুকিয়ে রাখতেন। তিনি নিজেকে নিজেই ক্ষুদ্র রাবণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। দুষ্টুমির মাঝেও তিনি স্নেহপ্রবণ ছিলেন। নানাস্তরের মানুষের জীবন প্রত্যক্ষ করে তিনি তার রচনায় তুলে ধরেছেন। যেমন সাপ খেলানো, গঙ্গার দূরন্ত স্রোতে নৌকা বাওয়া, বাড়ি থেকে পালিয়ে গ্রামগঞ্জে ঘুরে নানান অভিজ্ঞতা অর্জন বা বন্ধু রাজুর সঙ্গে ডিঙিতে চড়ে গঙ্গার বুকে নৈশ অভিযানের রহস্যগল্প সবই আমরা তার গল্পে পাই। রাজুর প্রতিচ্ছায়ায় তার লেখায় গড়ে ওঠে শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্রের কালজয়ী ঔপন্যাস ‘শ্রীকান্ত’। শ্রীকান্ত উপন্যাসে একটি ঘটনার বর্ণনা আছে গঙ্গায় ভেসে আসা একটি শিশুর মৃতদেহ নিয়ে কয়েকটি জন্তু-জানোয়ার টানাটানি করছে। সেই দৃশ্য দেখে অকুতোভয় ইন্দ্রনাথের চোখেও জল এসে গিয়েছিল। শ্রীকান্তকে ইন্দ্রনাথ মৃতদেহটি ধরার জন্য বললে শ্রীকান্ত সেটি ধরতে বা ছুঁতে দ্বিধা করছিল। ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তকে বললো ‘আরে এ যে মড়া, মড়ার আবার জাত কী? এই যেমন আমাদের ডিঙিটা-এর কী জাত আছে? আমগাছ, জামগাছ যে কাঠেরই তৈরি হোক-এখন ডিঙি ছাড়া একে কেউ বলবে না-আমগাছ জাম গাছ-বুঝলি না? এও তেমনি।’
শরৎচন্দ্রের বাবা ছিলেন প্রচুর বইপড়–য়া। সাহিত্যানুরাগী হওয়ায় তার বাবার আলমারিতে ছিল অনেক বইপত্র। স্কুলে থাকতেই সেখান থেকে লুকিয়ে গল্পের বই নিয়ে পড়তেন তিনি। এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন, “এবার আর বোধোদয় নয়, বাবার ভাঙ্গা দেরাজ থেকে খুঁজে বের করলাম হরিদাসের গুপ্তকথা’ আর বেরলো ভবানী পাঠক’। গুরুজনদের দোষ দিতে পারিনে, স্কুলের পাঠ্য ত নয়, ওগুলো বদছেলের অপাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই করে নিতে হলো আমাকে বাড়ীর গোয়াল ঘরে।”
তার বাবা সাহিত্য রচনা করতেন। সেসব লেখাও শরৎচন্দ্র পড়তেন আর ভাবতেন। এ নিয়ে তিনি ‘আত্মকথা’য় লিখেছেন, “আমার পিতার পান্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনটাই তিনি শেষ করতে পারেন নি। তাঁর লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই কবে কেমন করে হারিয়ে গেছে, সে কথা আজ মনে পড়ে না। কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় কতবার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কেন তিনি এগুলি শেষ করে যান নি, এই বলে কত দুঃখই না করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে, ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধ হয়, সতের বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে শুরু করি।”
সেসময়ে কয়েকজন সমবয়সী সাহিত্যানুরাগীদের নিয়ে শরৎচন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন সাহিত্যসভা। সে সাহিত্য সভায় তিনিই ছিলেন সভাপতি। সাহিত্য-সভার মুখপত্র ছিল হাতে লেখা পত্রিকা ‘ছায়া’।
এ সময়ে শরৎচন্দ্র প্রচুর পড়তেন এবং লিখতেন। এই চর্চাই গড়ে তুলেছিল পরবর্তীকালের কালজয়ী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। এ প্রসঙ্গে তার ৬২তম জন্মবার্ষিকীতে এক বেতার অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন, “আমার নিজের সাহিত্য–সাধনার ব্যাপার নিজের মুখে কিছু বলা যায় না। শুধু এইটুকুই ইঙ্গিতে বলতে পারি যে, অনেক দুঃখের মধ্য দিয়ে এই সাধনায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছি। কোনদিনই মনে করিনি যে, আমি সাহিত্যিক হবো বা কোন বই আমার কোনদিন প্রকাশিত হবে। এর মধ্যে যাঁরা আমার কথা শুনছেন, তাঁদের মধ্যে যদি কেউ সাহিত্যচর্চা করেন, অন্ততঃ সাহিত্যকে যদি তিনি অবলম্বন করেন, এই যদি তাঁর মনের বাসনা থাকে এবং সঙ্কল্পও যদি তাঁর স্থায়ী থাকে, তবে এই জিনিসটাকে তাঁকে নিশ্চয়ই প্রতিদিন মনে রাখতে হবে যে, এ হঠাৎ কিছু একটা গ’ড়ে ওঠবার জিনিস নয়।”
সে সময়কালে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। এক আড্ডায় শরৎচন্দ্র নিজের মুখেই নিজেকে বলেছিলেন ‘আমি চরিত্রহীন’। ১৯১৭ সালে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন তার বিখ্যাত উপন্যাস ‘চরিত্রহীন’। তখন ‘চরিত্রহীন’ মাত্রই বাজারে এসেছে। এসেই বাজিমাত। শুরু হয় আলোচনা-সমালোচনা, পাঠকদের মুখে মুখে শরৎচন্দ্রের নাম। এরই মধ্যে ‘কল্লোলিনী কলিকাতা’য় ঔপন্যাসিক হিসেবে আবির্ভূত হলেন আরেক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। চরিত্রহীন বের হওয়ার পরপর এই শরৎচন্দ্র বাজারে ছাড়লেন চাঁদমুখো নামে এক উপন্যাস। এই শরৎচন্দ্র আগে ছিলেন গল্পলহরী পত্রিকার সম্পাদক। লেখালেখি শুরু করেন পরে। কিš‘ একটা লিখে থামলে তো হয়, ওই শরৎচন্দ্র অতি দ্রæত লিখলেন তিনটি উপন্যাস চাঁদমুখো, হীরের দুল ও শুভলগ্ন। ফলে পাঠক-সমালোচকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল বিভ্রান্তিকে আসল আর কে নকল শরৎচন্দ্র। এ পরি¯ি’তিতে ‘বিরাট ফাঁপরে’ স্বয়ং ‘চরিত্রহীন’ শরৎচন্দ্রও ছিলেন। একদিন এক আড্ডায় তার সঙ্গে দেখা হলো এক বন্ধুর। বন্ধুটি বেজায় রসিক। রসিকতা করেই শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন, বাংলায় তো শরৎ এখন দুজন; তো হে, আপনি কোনজন?
শরৎচন্দ্রও ছিলেন বেশ রসিক। তাৎক্ষণিক তিনি জবাব দিলেন, ‘আমি “চরিত্রহীন” শরৎচন্দ্র!’ শরৎ সেদিন তার উপন্যাসের নামের সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করে বলেছিলেন বটে, তবে এরপর শরৎচন্দ্রের ‘চরিত্রহীন’ বিশেষণ আশপাশে বেশ ছড়িয়েছিল। নিজেকে নিয়ে তুমুল রসিকতা করতেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। একবার এক আসরে শরৎচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ বললেন, ‘তোমার জীবন সম্বন্ধে লোকের বড় কৌতূহল, আমার জীবনস্মৃতির মতন তোমার জীবনের কথা লেখো শরৎ!’
শরৎচন্দ্র কৌতুক করে বললেন, ‘না না, তা লেখা যায় না। আমার জীবন তো ভালো নয়। আগে বুঝতে পারিনি এত বড় হব, তবে নাহয় বুঝে-সুঝে ভালো হয়ে চলতাম।’
শরৎচন্দ্র প্রচুর ঘুরাঘুরি করতেন। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরাঘুরি করে মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তিনি তার লেখালেখিতে প্রয়োগ করতেন। ফলে তার লেখাগুলো হয়ে উঠতো জীবন্ত, তার লেখার ঘটনা ও চরিত্রগুলোতে তাই আমরা জীবনের প্রতি”ছবি দেখতে পাই। তিনি অসাম্প্রদায়িক ছিলেন এবং ধর্মীয় কুসংস্কার ও গোড়ামীর বিরুদ্ধে সবসময়ই ছিলেন সো”চার। এ ব্যাপারে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, ‘শরৎচন্দ্র বাঙালি দিয়ে ডুব দিয়েছিলেন। তার সৃষ্ট উপন্যাস ও গল্পে বাঙালি জীবনের পরিচয় সবচেয়ে স্পষ্টতায় বিমূর্ত হয়েছে। বাঙালি জীবনের যে ছবি তিনি এঁকেছেন তাতে কোন জাতিভেদ নেই।’
লেখক সত্তা ছাপিয়ে শরৎচন্দ্র হয়ে উঠেছিলেন বিপ্লবী। ১৯২১ সালে তিনি যোগ দেন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে। ১৯২১ থেকে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১৬ বছর ছিলেন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। শরৎচন্দ্রচরকায় খুব ভালো সুতো কাটতে পারতেন। একদিন গান্ধীজী তাকে প্রশ্ন করেন, ‘শরৎবাবু আপনার নাকি চরকায় বিশ্বাস নেই?’ উত্তরে শরৎবাবু বলেছিলেন, ‘না, আমি বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি স্বরাজ বা স্বাধীনতা আনবে সৈনিক, মাকড়সায় নয়। তবে যেহেতু আমি আপনাকে ভালোবাসি তাই চরকায় সুতো কাটি।’
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনের ওপর ভিত্তি করে শরৎচন্দ্র ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ‘পথের দাবি’ ঔপন্যাস রচনা করেন। ইংরেজ সরকার সেটি বাজেয়াপ্ত করে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ আনে। দরিদ্র দেশবাসীর জীবনের সমস্যার মূল, সমাধান দুটোই তিনি ধরতে পেরেছিলেন। শোষণের জন্যই শাসন, সেটা শরৎচন্দ্র জানতেন। এবং তিনি শোষিতের পক্ষ হয়েই কলম ধরেছিলেন।
শরৎচন্দ্রই প্রথম বাঙালি লেখক যিনি লেখাকেই একমাত্র পেশা হিসেবে গ্রহণ করে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তিনি আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন কালজয়ী কিছু সৃষ্টিকর্ম। ‘শ্রীকান্ত’, ‘গৃহদাহ’, ‘দত্তা, ‘নারীর মূল্য’, ‘শেষের পরিচয়’, ‘শেষ প্রশ্ন’, ‘অরক্ষণীয়া’, ‘একাদশীবৈরাগী’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তার অসাধারণ রচনাশৈলীতে বাংলা সাহিত্য পেয়েছে ‘পন্ডিতমশাই,’ নিস্কৃতি’, বৈকুণ্ঠের উইল’, বিরাজ বৌ’ উপন্যাসসহ বহু গল্প।
সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত শরৎচন্দ্র এখনো প্রাসঙ্গিক। নিজের সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে তিনি এখনো সাহিত্য ও পাঠকমহলে আবেদন রেখে চলছেন। কালান্তরে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা -এটাই একজন লেখকের সার্থকতা। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল ধ্রæবতারা। তার জীবনী ও সৃষ্টিকর্ম বর্তমান প্রজন্মের সামনে এগোতে প্রেরণার প্রতীক।
লেখক : শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।